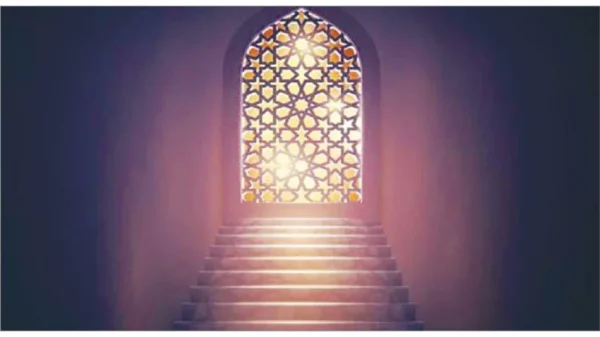বুধবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৫:৩৭ পূর্বাহ্ন
বাঁচতে হলে প্রতিরোধ ছাড়া উপায় কী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী:
কিশোররা এখন স্মার্ট হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে। স্মার্টনেস দেখিয়ে তারা হতাশ, বিষণœ, অপরাধপ্রবণ, নেশায় আকৃষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে বসে আছে বিদ্যমান ব্যবস্থার কাছে। আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে আত্মহত্যা; যা ঘটছে, দেখতে পাচ্ছি। যথার্থ স্মার্টনেস অবশ্য পোশাক-আশাক, চালচলন, ভাবভঙ্গির ওপর নির্ভর করে না, তার নির্ভরশীলতা ভেতরের সারবস্তুর ওপর। আর ওই সারবস্তুটি হচ্ছে জ্ঞান।
কোনো এক প্রকারের জ্ঞান নয়, নানাবিধ জ্ঞান। যেসব জ্ঞানের মধ্যে কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ থাকা অত্যাবশ্যক। কিশোরদের আমরা বঞ্চিত করছি উপকারী প্রায় সবরকমের জ্ঞান থেকেই। ওদিকে জ্ঞান আবার কেউ একাকী সংগ্রহ করতে পারে না, সামাজিক উদ্যোগ আবশ্যক; সেই উদ্যোগটিই এখন দেখা যাচ্ছে না।
এ দেশে এককালে কিশোর সংগঠন ও আন্দোলনের কাজকর্ম ছিল। এখন তা চোখে পড়ে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারকালে মুকুল ফৌজ ছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও সংগঠনটির অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত। সেটি এখন নেই। পাকিস্তান আমলে খেলাঘর ছিল বামপন্থিদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন, এখন আছে কি না বোঝাই যায় না। কচিকাঁচার মেলা ছিল একটি বড় সংগঠন। এদের কর্মসূচি বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কচিকাঁচার মেলাও এখন মৃতপ্রায়।
কিন্তু কিশোরদের যথার্থ স্মার্ট করা চাই। এবং করতে হলে, দেশজুড়ে একটি কিশোর আন্দোলন আজ খুব প্রয়োজন। কিশোরদের ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারলে, তাদের কাজ মানুষের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের বিকাশকে সহায়তা দেবে। অর্থাৎ আত্মসমর্পণের বিপরীতে সমাজ-পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করবে।
কিশোররা তখন আধুনিক হবে, কিন্তু পুঁজিবাদী হবে না। কিশোরদের জন্য গড়া এই আন্দোলন মোটেই আদর্শ-নিরপেক্ষ হবে না; তার আদর্শটা হবে রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক করা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক করে তোলা।
সেই রকমের একটি রূপান্তরের জন্য দরকার একটি সামাজিক বিপ্লবের। তবে সচেতন থাকতে হবে এ বিষয়ে যে, বিপ্লব যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে না এগোয় তাহলে তা কব্জায় চলে যাবে প্রতিবিপ্লবীদের, ইরানে যেমনটা ঘটেছে।
স্লোগানেরও যে বিপুল ক্ষমতা আছে, এক যুগ আগে আমাদের এই ঢাকা শহরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেøাগান দিয়েছে তরুণরা, যুদ্ধাপরাধীদের যথার্থ বিচার ও বিচারের রায় কার্যকর করার পক্ষে। সেøাগানমুখর আন্দোলনটি ব্যর্থ হয়নি; কিন্তু তাতে রাষ্ট্র ও সমাজে কোনো মৌলিক পরিবর্তন কিন্তু ঘটেনি, তার প্রতিক্রিয়াতে প্রতিক্রিয়াশীলরাই বরং সংঘবদ্ধ হওয়ার একটা মওকা খুঁজে পেয়েছে।
আজ প্রয়োজন আত্মসমর্পণের নয়, তার উল্টো যে পথ, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের পথ, সেটিকে বেগবান করা। সেটাই হচ্ছে জীবনের পথ, মৃত্যুর বিপরীতে।
কারা করবেন এ কাজ? করবেন হৃদয়বান ও বিবেকবানরা। কাজটি সব দেশেই প্রয়োজন হবে, বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে আমাদের মতো দেশে, যেখান থেকে সম্পদ অবাধে ও অবিরাম পাচার হয়ে যায়, যেখানে দুর্নীতির মাত্রা কমে না বাড়তেই থাকে, ফেসবুক ব্যবহারের যেটি শীর্ষ তিন দেশের মধ্যে স্থান করে নেয়। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের এমন যে অবস্থা তাতে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, আগামীতে শ্রেণি থাকবে মাত্র দুটিই, সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবঞ্চিত এবং পথও দাঁড়াবে দুটিই হয় আত্মসমর্পণ, নয় প্রতিরোধী। বাঁচতে হলে প্রতিরোধ ছাড়া উপায় কী?
করোনার কালে ও কারণে অনেক মানুষই আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার ঘটনা এখনো কমছে না, বাড়ছেই। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, দেশের ৩ কোটি মানুষই মানসিক রোগে আক্রান্ত। এবং এমন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে, মানসিকভাবে অসুস্থদের শতকরা ৯৪ জনই চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ১৭ কোটির ভেতর ৩ কোটিই যদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই যদি চিকিৎসা লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে অবস্থাটাকে নিশ্চয়ই সুখবর বলা যাবে না।
রোগগ্রস্ত ওই মানুষদের কেউই কিন্তু মানসিক অসুখ নিয়ে জন্মায়নি, জন্মের পরেই তারা অসুস্থ হয়েছে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে। আর এই রুগ্্ণ মানুষেরা যে চিকিৎসা পায় না তার কারণ চিকিৎসা-ক্রয়ে তাদের সামর্থ্যরে অপ্রতুলতা। জরিপ বলছে চিকিৎসা ব্যয়ের শতকরা ৬৯ ভাগ এখন ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়।
বহন করার ওই ক্ষমতা বেশির ভাগ মানুষেরই যে নেই সেটা তো নিষ্ঠুর এক সত্য। সরকারি চিকিৎসালয় কিছু আছে, তার খরচ জনগণকেই বহন করতে হয়, কিন্তু এখন এমন ধারণা সঙ্গতকারণেই জন্ম লাভ করেছে যে, ওইসব চিকিৎসালয়ে সবকিছুই পাওয়া সম্ভব, চিকিৎসা ছাড়া। অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই, কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।
আর সরকারি হাসপাতালেও এখন যে চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব সেটা পেতে হলে যে নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হবে, এমন ব্যবস্থা নাকি জারি হয়েছে। গুঞ্জন আগেই শোনা গেছিল, এখন তা সত্য হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এখন থেকে ওই হাসপাতালেই এবং সরকার প্রদত্ত তাদের চেম্বার ব্যবহার করেই প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবেন।
সকালে রোগী দেখবেন বিনা পয়সায়, বিকেলে দেখবেন নগদ অর্থের বিনিময়ে। সকালে আসবে বিত্তহীনরা, তাদের সংখ্যা হবে অধিক; বিকেলে দেখা দেবে অবস্থাপন্নরা, তাদের সংখ্যা তুলনায় কম থাকবে, এবং চিকিৎসকরাও তাদের যথোপযুক্ত সময় দিতে পারবেন। একই হাসপাতালে দুরকম চিকিৎসা।
অবস্থাপন্ন রোগীরা অবশ্য তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না, তারা তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক চিকিৎসা পেয়ে যাবেন এবং ডাক্তারের খোঁজে তাদের এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।
সুযোগবঞ্চিত রোগীরা? তারা মরুক গে, তাদের নিয়ে কার অত মাথা ব্যথা? সবকিছুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা এমনটাই। তবে এতে হতাশা বৃদ্ধি পাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়; সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছেও এবং তাতে শোক-দুঃখ তো বটেই, আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।
মানুষের পিঠ যে দেয়ালে ঠেকে গেছে এবং যাচ্ছে, তার খবর হরদম পাওয়া যায়। আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে আগেও লিখেছি, এখানেও লিখতে হচ্ছে। ফারদিন যদি সত্যি সত্যি নিজেই নিজেকে খুন করে থাকে, তবে সেটা নিশ্চয়ই ঘটেছে চরম হতাশা থেকেই।
দুঃসহ দারিদ্র্য কখনো কখনো অবশ্যই আত্মহত্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়। যেমন রোজিনা বেগমের বেলাতে ঘটেছে। মানিকগঞ্জের ঘিওরে তার বসবাস। একেবারে হতদরিদ্র যে ছিলেন তা নয়। এক সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।
কিন্তু দুই সন্তান রেখে স্বামী মারা যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েন। তবু ভেঙে পড়েননি। আট লাখ টাকা দাম ঠিক করে একটা ট্রাক কিনেছিলেন, একজনের কাছ থেকে। অর্ধেক টাকা মিটিয়েছেন, অর্ধেকটা বাকি। কিছুদিন পর আরেক ব্যক্তি এসে হাজির, তার দাবি ট্রাকটি তার, কারণ সেটি তিনি কিনেছেন, এবং প্রমাণ হিসেবে দলিলও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে।
রোজিনা বেগম তখন অতল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন। ধারণা করা হয়, ট্রাক কেনার অর্ধেক টাকাটা তিনি কোনো এনজিওর কাছ থেকে কর্জ করেছিলেন। চাপ ছিল কিস্তি শোধের। প্রতিবেশীরা দেখতেন, রোজিনা বেগম খুবই বিষণœ থাকেন, কিন্তু তিনি যে কীটনাশক খেয়ে প্রাণবিসর্জন দেবেন এটা কেউ ভাবেননি।
অথচ ঠিক সেটাই ঘটেছে। অভাবের বোঝা বহনে অক্ষম হয়ে তিনি মুক্তির জন্য কোনো পথ খুঁজে পাননি, আত্মহনন ভিন্ন। তার সন্তান দুটির কী হবে কে জানে।
লেখকঃ ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়